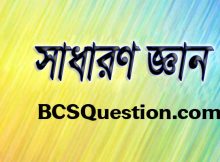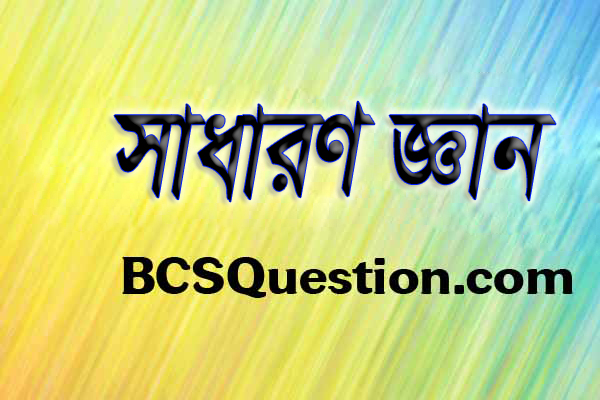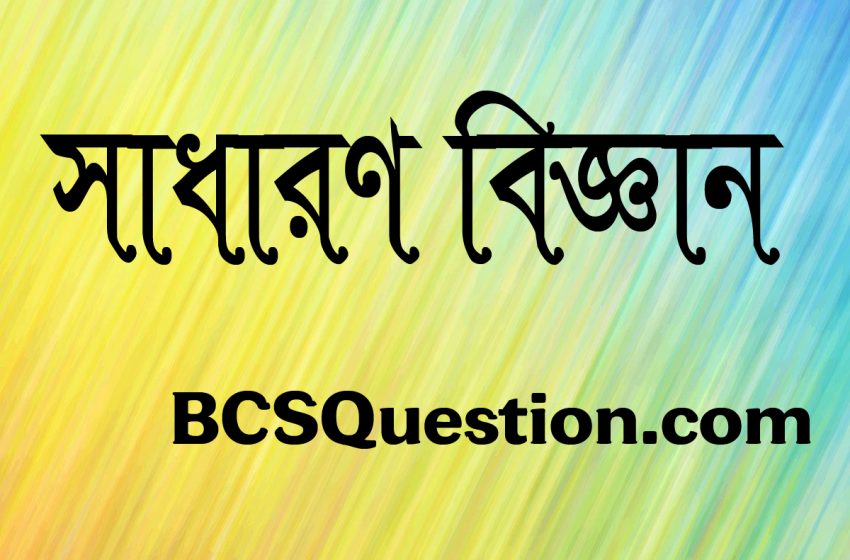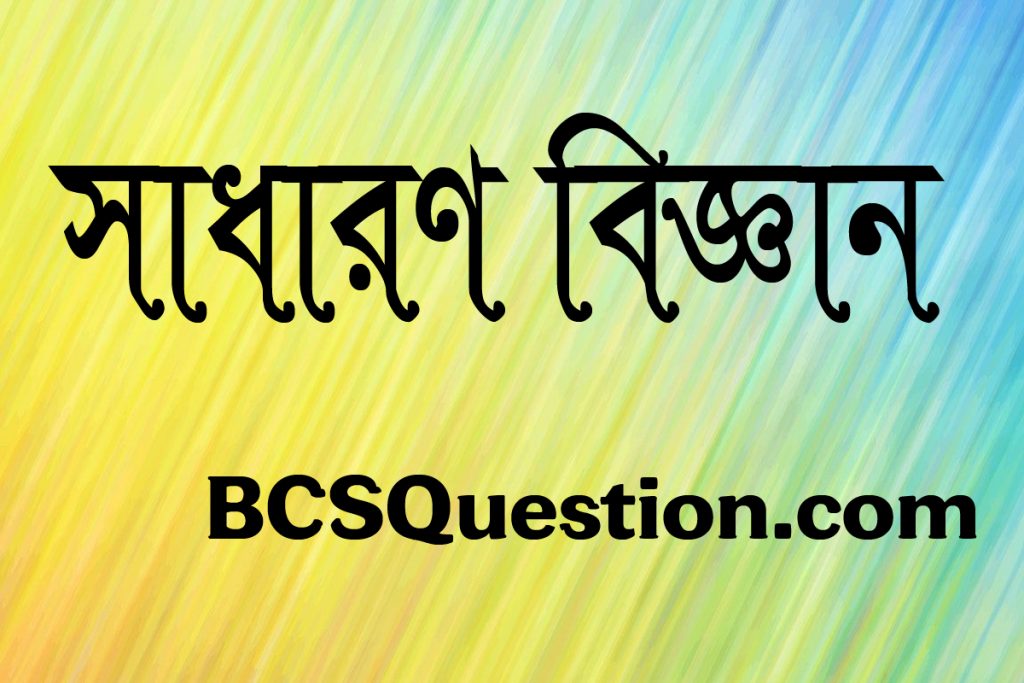বাংলায় আফগান শাসনাবসানের পর শুরু হয় মুঘল শাসন। সুবাদারী ও নবাবী এ দুই পর্বে বাংলায় প্রায় দুইশ বছরের মুঘল শাসন অতিবাহিত হয়। ১৫৭৬-১৭১৭ সাল পর্যন্ত মুঘল আমল সুবাদারী শাসন নামে অভিহিত। বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে মুঘল সুবাদারী শাসন এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়।
সুবাদারী শাসন
মুঘল প্রদেশগুলো সুবাহ্ নামে পরিচিত ছিল। বাংলা ছিল মুঘলদের অন্যতম প্রদেশ বা সুবাহ্। আকবর তার সাম্রাজ্যকে ১২টি সুবাহয়ে বিভক্ত করেন। সুবাসমূহ এলাহাবাদ, আগ্রা, অযোধ্যা, আজমীর, আহমেদাবাদ, বিহার (রাজধানী পাটনা), বাংলা (রাজধানী রাজমহল), দিল্লি, কাবুল, লাহোর, মুলতান এবং মালওয়া। সুবাহুসমূহের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রশাসকদের বলা হতো সুবাদার। সুবাদার অর্থ সুবাহ্’র রক্ষক বা শাসক । প্রকৃতপক্ষে সুবাদারেরা সম্রাটের প্রতিনিধিরূপে সুবাহ্ শাসন করতেন।
এই বিভাগের আরো পোস্ট :
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দ্বিতীয় গ্রন্থ কারাগারের রােজনামচা
- শতবর্ষে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
- করোনা ভাইরাস সম্পর্কিত জানা অজানা তথ্য [পিডিএফ]
- মার্চ মাসের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ
বাংলায় সুবাদারী শাসন
১৫৩৮ সালে সম্রাট হুমায়ুন বাংলার রাজধানী গৌড় অধিকার করে মুঘল শাসনের সূচনা করেন । কিন্তু শের শাহ শূরির কারণে বাংলায় মুঘল রাজত্ব বাধাগ্রস্ত হয়। পরবর্তীতে আকবরের শাসনামলে ১৫৭৬ সালে দাউদ খান কররানীর পরাজয়ের পর বাংলায় প্রকৃত মুঘল শাসনের সূত্রপাত হয় ।
এই বিভাগ থেকে আরো পড়ুন
- বিসিএস প্রিলিমিনারি প্রস্তুতি সাধারণ জ্ঞান বাংলাদেশ বিষয়াবলী
- মৌলভীবাজার জেলার নামকরণ, ইতিহাস, দর্শনীয় স্থান, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি
- ১৯৭১ : দ্য শিলিগুড়ি কনফারেন্স’ : মুক্তিযুদ্ধের অনুদঘাটিত এক দলিল
- বিসিএস প্রস্তুতি (Bcs Preparation) : প্রশ্নোত্তরে একাত্তর (১৯৭১)
- জাতি ও রাষ্ট্র সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর
- বারাে ভূঁইয়া : ইতিহাসের গৌরবােজ্জ্বল অধ্যায়
- সুনামগঞ্জ জেলার নামকরণ, ইতিহাস, দর্শনীয় স্থান, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি
- সাতক্ষীরা জেলার নামকরণ, ইতিহাস, দর্শনীয় স্থান, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি
- খুলনা জেলার নামকরণ, ইতিহাস, দর্শনীয় স্থান, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি
- মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র
তখন থেকে বাংলায় মুঘল সুবাদারী শাসন শুরু হলেও সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে বাংলায় সুবাদারদের কর্তৃত্ব ছিল একেবারেই সীমিত। সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলে মুজাদ্দিদে আলফিসানীর অন্যতম অনুসারী সুবাদার ইসলাম খান ১৬১০ সালে বারো ভূঁইয়াদের পরাজিত করে সমগ্র বাংলায় সুবাদারী শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। সুবাদার ইসলাম খান ঢাকাকে সুবাহ্ বাংলার রাজধানী হিসেবে ঘোষণা দিয়ে এর নাম রাখেন জাহাঙ্গীরনগর। কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট সুবাহ্ বাংলা পৃথক গুরুত্ব পেত। বাংলার সুবাদারের পদ খালি হলে বিহারের সুবাদারকেই বাংলার সুবাদারের পদ প্রদানের প্রথা আকবরের সময় থেকে প্রচলিত হয়।
মুঘল আমলে বাংলার রাজধানী
| রাজধানী | স্থানান্তর/প্রতিষ্ঠা | স্থানান্তরকারী |
| তাণ্ডা | ১২ জুলাই ১৫৭৬ | – |
| রাজমহল | ৭ নভেম্বর ১৫৯৫ | মানসিংহ |
| ঢাকা | ১৬ জুলাই ১৬১০ | ইসলাম খান চিশতি |
| রাজমহল | ১৬৫০ সালে | শাহ্ সুজা |
| ঢাকা | ১৬৬০ সালে | মীর জুমলা |
| মুর্শিদাবাদ | ১৭১৭ সালে | মুর্শিদকুলী খান |
উল্লেখ্য, স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী হওয়ার পূর্বে ঢাকা ১৬১০, ১৬৬০, ১৯০৫ ও ১৯৪৭ সালে মোট ৪ বার বাংলার রাজধানী হয়।
গুরুত্বপূর্ণ সুবাদারগণ
শাহ্ সুজা
শাহ্ সুজা ছিলেন সম্রাট শাহজাহান ও সম্রাজ্ঞী মমতাজ মহলের দ্বিতীয় পুত্র। ১৬৩৯ সালে সম্রাট শাহজাহান শাহ্ সুজাকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন। শাহ্ সুজা জ্ঞানী, সংস্কৃতিবান ও কেতাদুরস্ত আদর্শ শাসক ছিলেন। তিনি বড় কাটরা, ধানমন্ডির শাহী ঈদগাহ, লালবাগ মসজিদ ও চুড়িহাট্টা মসজিদ নির্মাণ করেন । ১৬৫৭ সালে সম্রাট শাহজাহান অসুস্থ হয়ে পড়লে তার চার পুত্রের প্রত্যেকেই সম্রাট হওয়ার জন্য বিদ্রোহ করে । এ সময় আওরঙ্গজেবের সাথে শাহ্ সুজার দ্বন্দ্ব শুরু হয়। দুই ভাইয়ের যুদ্ধে ১৬৫৯ সালে শাহ্ সুজা পরাজিত হন এবং আরাকানে পলায়ন করেন। পরে সেখানেই সপরিবারে নিহত হন ।
মীর জুমলা
ইস্পাহানের আর্দিস্তানে ১৫৯১ সালে মীর জুমলার জন্ম হয় । প্রথম জীবনে তিনি হীরার ব্যবসার সাথে জড়িত ছিলেন। ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে তিনি ভারতে আগমন করেন। মুঘল সুবাদার শাহজাদা আওরঙ্গজেবের সাথে তার সখ্য তৈরি হয় । আওরঙ্গজেব সম্রাট হওয়ার পর ১৬৬০ সালে বাংলার সুবাদার হিসেবে নিযুক্ত হন মীর জুমলা। তার বড় সাফল্যগুলোর মধ্যে অন্যতম কামরূপ ও আসাম রাজ্য দখল করা। আসামের যুদ্ধে তার ব্যবহারকৃত কামান বর্তমানে ওসমানী উদ্যানে সংরক্ষিত আছে ।
শায়েস্তা খান
১৬৬৩ সালে সম্রাট আওরঙ্গজেব শায়েস্তা খানকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন। শায়েস্তা খান ছিলেন সম্রাট আওরঙ্গজেবের মামা ও সম্রাট শাহজাহানের স্ত্রী মমতাজের ভাই। প্রথমে ১৬৬৪-১৬৭৮ সাল পর্যন্ত তিনি বাংলার সুবাদার ছিলেন। ১৬৭৮ সালে সম্রাট আওরঙ্গজেবের পুত্র মুহাম্মদ আজম বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হওয়ার পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাদের হীনস্বার্থ বাস্তবায়নের জন্য মুহাম্মদ আজমকে ২১,০০০ টাকা ঘুষ প্রদান করে।
সম্রাট আওরঙ্গজেব তা জানতে পেরে তাকে পদচ্যুত করে পুনরায় শায়েস্তা খানকে বাংলায় প্রেরণ করেন। তিনি এক বছরেরও কম সময়ের ব্যবধানে দ্বিতীয়বার নিযুক্ত হয়ে ১৬৮৮ সাল পর্যন্ত বাংলার সুবাদারী করেন। ফরাসি পর্যটক বার্নিয়ার শায়েস্তা খানের আমলে বাংলার প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্যের বিশদ বিবরণ দেন । তার সময়ে খাদ্যশস্যের মূল্য এত সস্তা হয় যে, টাকায় ৮ মণ চাল পাওয়া যেত। শায়েস্তা খান ছোট কাটরা, চকবাজার মসজিদ, লালবাগ দুর্গের পরীবিবির মাজার, রায়ের বাজারের সন্নিকটে সাত গম্বুজ মসজিদ ইত্যাদি ইমারত নির্মাণ করেন।
সুবাদারী আমলে বাংলায় আগত বিদেশি পর্যটক
| নাম | দেশ | আগমন |
| রালফ ফিচ | ইংল্যান্ড | ১৫৮৬ |
| সেবাস্টিন মানরিক | পর্তুগাল | ১৬২৮ |
| নিকোলা মানুচি | ইতালি | ১৬৬৩ |
| টাভার্নিয়ার | ফ্রান্স | ১৬৬৬ |
| ফ্রান্সিস বার্নিয়ার | ফ্রান্স | ১৬৬৬ |
মগ, ফিরিঙ্গি, হার্মাদ দমন
বাংলায় মুঘল শাসনের সূচনার দিকে, যখন বারো ভূঁইয়ারা দুর্বল ছিল এবং মুঘলরাও নিজেদের ক্ষমতা শক্ত করতে পারেনি, সে সময় বর্তমান মিয়ানমারের মগ দস্যু ফিরিঙ্গি ও পর্তুগিজ জলদস্যুরা মিলিত হয়ে প্রায়ই বাংলার দক্ষিণাঞ্চলীয় উপকূলে হানা দিত এবং প্রচুর ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করে নিয়ে যেত। মগ ও পর্তুগিজ ফিরিঙ্গিদের একসাথে হার্মাদও বলা হতো। পর্তুগিজ পাদরিরাও জড়িত ছিল এসব দস্যুতার সাথে। একসময় তাদের দৌরাত্ম্য ঢাকা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। ১৬২৫ সালে মগরাজ শ্রীসুধর্ম ঢাকায় আক্রমণ করে তিনদিন ধরে শহরে নির্মম লুণ্ঠন ও হত্যাযজ্ঞ চালায়। শায়েস্তা খান মগদের দমনের চূড়ান্ত পদক্ষেপ নেন । ১৬৬৬ সালে তিনি ‘চট্টগ্রাম জয় করার পর মগদের ঝোঁটিয়ে বিদায় করেন। তাদের এ পলায়নই ইতিহাসে মগ ধাওনী নামে পরিচিত। এইভাবে গোটা বাংলায় মগের মুল্লুক-এর অবসান ঘটে।
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও স্বাধীনতার মৃত্যুপরওয়ানা
১৬০০ সালে ভারত ও পূর্ব এশিয়ায় বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ডের একদল বণিক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠন করেন তারা ১৬১২ সালে মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনকালে ভারতের সুরাটে প্রথম বাণিজ্য কুঠি স্থাপনের অনুমতি পায় ৷ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৬৩৩ সালে মহানন্দা বদ্বীপের হরিহরপুরে একটি ফ্যাক্টরি স্থাপনের মাধ্যমে বাংলায় ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করে। এক পর্যায়ে তারা বর্ণহিন্দু ব্যবসায়িক মিত্রদের সহযোগিতা নিয়ে এদেশের রাজনীতির দিকে হাত বাড়াতে শুরু করে। এরপর বাণিজ্যিক শর্ত লঙ্ঘন, সৈন্য ও অস্ত্র সমাবেশ, দুর্গ নির্মাণ, কর প্রদানে কারচুপি, দেশীয় ব্যবসায়ীদের সাথে সংঘর্ষ নিত্যদিনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। প্রাথমিক পর্যায়ে ইংরেজরা সম্রাট শাহজাহান ও বাংলার সুবাদার শাহ সুজার উদারতায় বাংলায় অবাধে বাণিজ্যের সুযোগ পায়। কিন্তু তাদের সেই উদারতাকে অকৃতজ্ঞ ইংরেজ বণিকগণ পরবর্তীকালে মুঘল সাম্রাজ্যের ও বাংলা-বিহারের স্বাধীনতার মৃত্যু পরোয়ানা হিসেবে ব্যবহার করে।
চাইল্ডের যুদ্ধ
১৬৮৭ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কোর্ট অব ডাইরেক্টর্স মাদ্রাজের গভর্নরকে এমন একটি বেসামরিক ও সামরিক শক্তির সংগঠন গড়ে তুলতে এবং এর নিরাপত্তার জন্য বিরাট অঙ্কের রাজস্ব সংগ্রহ করতে নির্দেশ দেন যাতে এ সংগঠন সর্বকালের জন্য ভারতে একটি বিশাল, সুদৃঢ় ও নিরাপদ ইংরেজ রাজ্যের অংশ হয়ে উঠতে পারে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সবচেয়ে প্রভাবশালী পরিচালক জসিয়া চাইল্ড এ নতুন নীতি নির্ধারণে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন । এ জঙ্গি নীতির কারণে ১৬৮৬ সালে মুঘল প্রশাসনের সঙ্গে কোম্পানির যুদ্ধ বাঁধে। শেষ পর্যন্ত কোম্পানি মুঘল সাম্রাজ্যের সশস্ত্র বাহিনীর কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয় এবং কোম্পানিকে ১,৫০,০০০ টাকা জরিমানা করা হয় ।
সুবাদারী শাসন ব্যবস্থা
মুঘল সুবাদারী শাসনামলে বাংলা কেন্দ্রের অধীনে থাকলেও এর আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন নতুন গতি লাভ করে ছিল। এ সময় নানা অর্থনৈতিক পণ্য উৎপাদন যেমন হয়েছিল তেমনি স্থানীয় পণ্যের উৎকর্ষতার সুযোগে এর অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্যও প্রসারিত হয়েছিল। ইউরোপবাসীরা বাংলাকে পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী বাণিজ্য দেশ হিসেবে গণ্য করতো। সেসময় তারা মুঘল বেঙ্গলকে প্যারাডাইস অব নেশনস এবং বাংলার স্বর্ণযুগ হিসেবে বর্ণনা করে। এছাড়া জনজীবনে শান্তি ও সমৃদ্ধি থাকায় শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল। এ সময় সকল ধর্মালম্বী ব্যক্তিবর্গ স্বাধীনভাবে স্ব স্ব ধর্ম পালন করতে পারতেন।
বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় আসা প্রশ্নোত্তর
প্রশ্ন : ‘সুবা বাংলা’ শব্দটি প্রথম ব্যবহার করা হয়
উত্তর : সম্রাট আকবরের সময়ে। (জাবি ১৩-১৪)
প্রশ্ন : কার সময়ে বাংলার রাজধানী ঢাকায় স্থাপন করা হয়?
উত্তর : সম্রাট জাহাঙ্গীর। (প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক ৯৩)
প্রশ্ন : ঢাকা কখন সর্বপ্রথম বাংলার রাজধানী হয়েছিল?
উত্তর : ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে। (২৮তম, ২১তম বিসিএস)
প্রশ্ন : সম্রাট শাহজাহানের কোন পুত্র বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন?
উত্তর : শাহ সুজা। (CGDF জুনিয়র অডিটর ১৪)
প্রশ্ন : ‘ঢাকা গেট’ কে নির্মাণ করেন?
উত্তর : মীর জুমলা। (জিবি ০৮-০৯)
প্রশ্ন : শায়েস্তা খানের আমলে এক টাকায় চাউল পাওয়া যায়
উত্তর : ৮ মণ। (রাবি (A-1) ১২-১৩)
প্রশ্ন : ঢাকার ‘ধোলাই খাল কে খনন করেন?
উত্তর : ইসলাম খান । (৩৬তম বিসিএস, ঢাবি ‘চ’ ইউনিট ১৭-১৮)
প্রশ্ন : ঢাকায় বাংলার রাজধানী স্থাপনের সময় মুঘল সুবাদার কে ছিলেন?
উত্তর : ইসলাম খান । (২৬তম বিসিএস)
প্রশ্ন : কোন মুঘল সুবাদার চট্টগ্রাম দখল করে এর নাম রাখেন ইসলামাবাদ?
উত্তর : শায়েস্তা খান। (প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক ১২)
প্রশ্ন : পরীবিবি কে ছিলেন?
উত্তর : শায়েস্তা খানের কন্যা। [প্রাক- প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক ১৩ (বুড়িগঙ্গা)
প্রশ্ন : লালবাগ দুর্গের অভ্যন্তরের সমাধিতে সমাহিত শায়েস্তা খানের এক কন্যার আসল নাম
উত্তর : ইরান দুখত। (১৭তম বিসিএস)
প্রশ্ন : লালবাগের কেল্লা স্থাপন করেন কে?
উত্তর : শায়েস্তা খান। (১৬তম বিসিএস, প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক ০২)
প্রশ্ন : মীর জুমলার কামানটি কোন যুদ্ধে ব্যবহৃত হয়?
উত্তর : আসাম যুদ্ধে। (পরিসংখ্যান ব্যুরোর জুনিয়ার পরিসংখ্যান সহকারী ১৬)